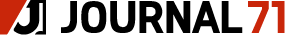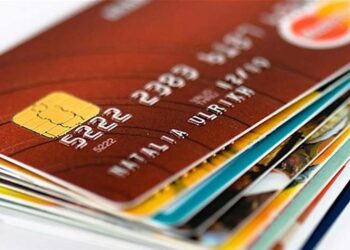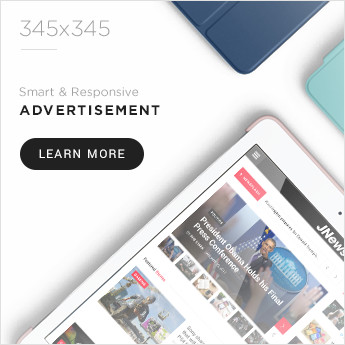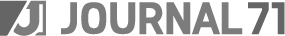বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি এখন এক বিশাল বৈপরীত্যের মুখোমুখি। একদিকে রফতানি ও প্রবাসী আয়ের ধারা শক্তিশালী হচ্ছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আগের তুলনায় স্থিতিশীল রয়েছে। তবে অন্যদিকে, দেশের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত বেসরকারি খাত গুরুতর সংকটে পদাঘাতপ্রাপ্ত। বিনিয়োগের ধারা থামছে, শিল্পোৎপাদন কমে যাচ্ছে, এবং এর ফলে কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়ে পড়ছে।
শিল্পখাতে অচলাবস্থা এখন সাধারণ ছবি। কারখানা মালিকরা জানাচ্ছেন, ব্যবসা-বাণিজ্য উপযোগী পরিবেশ এখন আগের চেয়ে বেশি প্রতিকূল। গ্যাস ও বিদ্যুতের সরবরাহ বিরত থাকছে, ব্যাংক থেকে ঋণের সুদের হার ১৬ শতাংশে উত্তরণ করছে। মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য এলসি খোলা কঠিন হয়ে যাচ্ছে, আর শিল্পে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও শ্রম আইন সংস্কারের বিষয়ে ব্যবসায়ীদের দুশ্চিন্তা দিন দিন বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন বিনিয়োগে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করছে না, বরং পুরোনো বিনিয়োগই হুমকির মুখে। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি হাজারো শ্রমিক চাকরি হারাচ্ছেন।
বৈঠক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতাদের মূল্যায়নে, ব্যাংক খাতের সমস্যা এক বড় বাঁধা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেছেন, ব্যাংক ঋণের জন্য অপ্রতুলতা ও আমদানির বিঘ্ন ঘটছে, যা অবিচ্ছিন্নভাবে বিনিয়োগের অন্তরায়। অন্যদিকে, বিজিএমইএর সভাপতি মো. শাহরিয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, অধিকাংশ ব্যবসায়ী এখন এলসি বা ঋণের খাত থেকে বঞ্চিত, যার ফলে তারা প্রয়োজনীয়ভাবে সুবিধা পেতে পারছেন না।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত আগস্টে আমদানির দায় পরিশোধের হার ১১ শতাংশ কমে ৪.৮৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। মূল কারণ হলো, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে হ্রাস, যার ফলে নতুন কারখানা ও শিল্প সম্প্রসারণ কার্যত বন্ধ। নতুন এলসি খোলা কিছুটা বেড়েছে, তবে তা মূলত ভোগ্যপণ্য আমদানির জন্য। অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিনিয়োগের কমতিসহ কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির চাহিদা কমে যাচ্ছে।
সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান উল্লেখ করেছেন, তৈরি পোশাক খাতের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির জন্য এলসি নিষ্পত্তির হার কিছুটা আশা জাগালেও, মূলধনী যন্ত্রের আমদানি কমে যাওয়ায় সামগ্রিক এলসি নিষ্পত্তি কমে গেছে। তিনি আরও বলেছেন, ‘‘মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানির হ্রাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় ব্যাংকঋণের প্রবৃদ্ধি থেকে, যা বর্তমানে ৬-৭ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবং এটি নতুন বিনিয়োগের অপ্রতুলতার প্রমাণ।’’
ঋণ প্রবৃদ্ধির রেকর্ডও দারুণ নিম্নগামী। চলতি বছর জুনে প্রাইভেট সেক্টরের ক্রেডিট প্রবৃদ্ধি ৬.৪৯ শতাংশের নিচে নেমে আসার পাশাপাশি, সরকারি খাতে এই হার ১৩ শতাংশের ওপরে। এর ফলে বেসরকারি খাত কার্যত ক্রাউড আউটের শিকার হচ্ছে, যেখানে ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনীয় ঋণ পাচ্ছেন না। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে শিল্প, কর্মসংস্থান ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর।
আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ নিয়ে গুরুতর অস্বস্তির কথা উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর ২০২৫ সালের বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রতিবেদনেও পাঁচটি মূল বাধার উল্লেখ করা হয়েছে: অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, সীমিত অর্থায়ন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, বৈষম্যমূলক কর কাঠামো ও দুর্নীতি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলেও বিনিয়োগ পরিস্থিতিতে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি।
অন্যদিকে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ অর্থনীতির বৃদ্ধির পূর্বাভাস কিছুটা কমিয়ে ৫ শতাংশ করেছে। তারা সতর্ক করে বলেছে, নতুন মার্কিন শুল্ক, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও ব্যাংক খাতের দুর্বলতা বিনিয়োগ ও রফতানি পরিস্থিতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে।
তবে সামান্য কিছু স্বস্তির খবর রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি আগস্টে ৯.৭ শতাংশে চলে এসেছে, যা গত দুই বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবন কিছুটা সহজ হয়েছে। কিন্তু রাজস্ব ঘাটতি বাড়ছে ও সরকারি ব্যয় কমে যাচ্ছে, ফলে অর্থনীতির অন্যান্য সূচক নড়বড়ে। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় মাসে অগ্রগতি মাত্র ২.৩৯ শতাংশ, যা সাম্প্রতিক বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বিনিয়োগ ফিরিয়ে আনতে তিনটি বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ জরুরি: রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, ব্যাংকিং খাতে আস্থা ফেরানো এবং নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। তারা সতর্ক করে বলছেন, এই সংকট দীর্ঘস্থায়ী হলে কর্মসংস্থান সংকট আরও গভীর হবে, এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে।